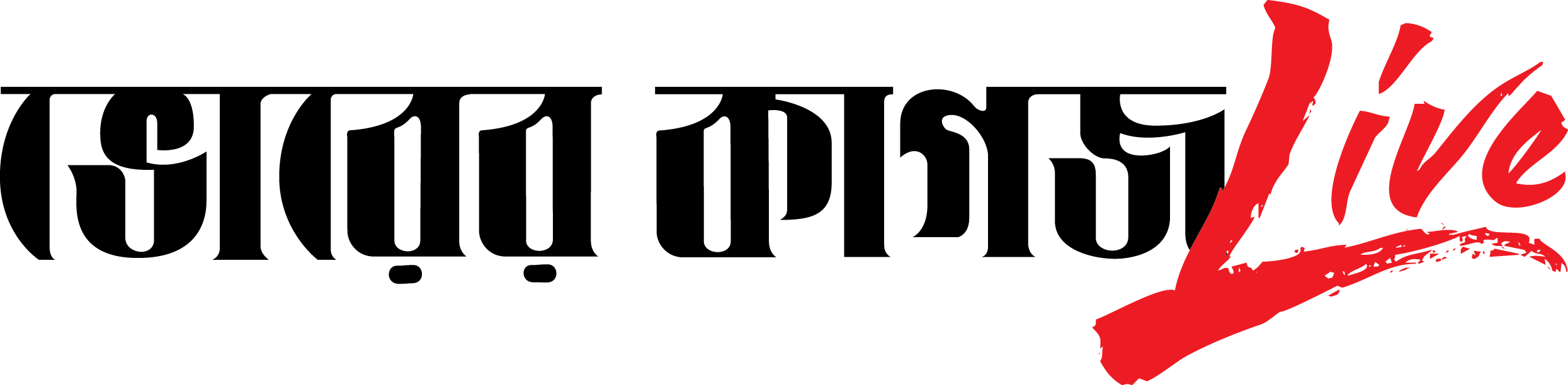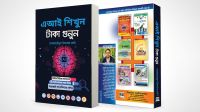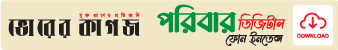সরকারি হাসপাতাল
ভোগান্তি পিছু ছাড়ে না রোগীর
সেবিকা দেবনাথ
প্রকাশ: ০২ নভেম্বর ২০২৫, ০৩:৫৯ পিএম

ছবি : সংগৃহীত
দেশের জনসংখ্যার বড় একটি অংশই চিকিৎসা নেন সরকারি হাসপাতালে। চলতি বছরের শুরুর দিকে প্রকাশিত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুযায়ী, গত এক বছরে ৬২ শতাংশ মানুষ সরকারি হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র থেকে সেবা নিয়েছেন। সরকারি হাসপাতালে সেবা নেয়ার হার শহরের চেয়ে গ্রামে বেশি। অথচ সেই হাসপাতালগুলোতেই অব্যবস্থাপনা সবচেয়ে বেশি। ওই জরিপের তথ্য বলছে, দেশের প্রতি ৩ জনের মধ্যে ১ জন মানুষের সরকারি বা বেসরকারি হাসপাতালে অবহেলা, অযত্ন ও অপচিকিৎসার শিকার হওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে। গ্রামের চেয়ে শহরে এই হার বেশি। দেশের ৩৮ শতাংশ মানুষ হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে গিয়ে অবহেলা, অযত্ন বা অপচিকিৎসার শিকার হন। গ্রামের ৩৬ শতাংশ মানুষ ও শহরের ৪৪ শতাংশ মানুষ এই অভিযোগ তুলেছেন।
তথ্য বলছে, সরকারি হাসপাতালের বহির্বিভাগেই অধিকাংশ জনগণ চিকিৎসা নেন। কিন্তু দেরিতে চিকিৎসক আসা, জনবল সংকট ও অধিকাংশ সময় যন্ত্রপাতি নষ্ট থাকায় যথাযথ চিকিৎসা পান না রোগীরা। এছাড়া রোগীর চাপে চিকিৎসকদের আন্তরিকতারও যায় কমে। অন্যদিকে দেশে রেফারেল পদ্ধতি না থাকায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রোগী ভুল করে অন্য রোগের বিশেষজ্ঞের কাছে চলে যান। তখন ভোগান্তি আরো বাড়ে।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, মুগদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, কুরমিটোলা জেনারেল হাসপাতাল, মিটফোর্ড মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রোগীর ভিড় যেমন আছে; তেমনি আছে নানা অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার অভিযোগও। বলা যায়, সব হাসপাতালের দৃশ্যপট একই। এসব হাসপাতালে বহির্বিভাগের টিকেট কাউন্টারের সামনে এবং টিকেট কাটার পর চিকিৎসক দেখানোর জন্য অপেক্ষা করতে হয় দীর্ঘক্ষণ। প্রহর গুণতে গুণতে ঘণ্টা পেরিয়ে যায়, রোগীর সারিও ধীরে ধীরে র্দীঘ হয়। তবে বিশেষায়িত হাপসাতাল যেমন- ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস অ্যান্ড হাসপাতাল, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, জাতীয় ক্যানসার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, জাতীয় কিডনি অ্যান্ড ইউরোলজি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে রোগীর ভোগান্তি যেন একটু বেশি।
নিউরোসায়েন্সেস হাসপাতালের টিকেট কাউন্টার থেকে শুরু করে বহির্বিভাগে থাকা চিকিৎসকের রুমের সামনে রোগীদের অপেক্ষা করতে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। শুধু তাই নয়, বেড সংকটে ফিরে যান অনেকেই। এমআরই, সিটিস্ক্যান কিংবা ভর্তির জন্য অপেক্ষা করতে হয় ২ থেকে ৩ মাস। স্নায়ু চিকিৎসায় একমাত্র বিশেষায়িত হাসপাতাল হওয়ায় সারাদেশের রোগীর চাপ সামলাতে রীতিমতো হিমশিম অবস্থা। চিকিৎসকরা বলছেন, গত ১৩ বছরে এই হাসপাতালে রোগীর চাপ বেড়েছে প্রায় ৬ গুণ। ফলে বহির্বিভাগে একজন চিকিৎসককে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২শ জন করে রোগী দেখতে হয়।
হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক ডা. কাজী গিয়াস উদ্দিন আহমেদ জানান, নতুন ভবন চালু হলে অভিযোগ ও সংকট অনেকাংশে কমে আসবে। সবকিছু ঠিক থাকলে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে নতুন ভবনের কার্যক্রম শুরু হবে বলেও জানান পরিচালক। যেখানে স্নায়ু রোগীদের জন্য থাকবে বিশ্বের অত্যাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম, পদ্ধতি ও প্রযুক্তির সমন্বয়।
একই অবস্থা জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে। হৃদরোগে আক্রান্তদের জন্য জেলাগুলোর সরকারি হাসপাতালে প্রয়োজনীয় সেবা নেই। ফলে রোগীদের সব চাপ ঢাকায়। আবার ঢাকায় সরকারিভাবে একমাত্র বিশেষায়িত হাসপাতাল জাতীয় হৃদরোগ হাসপাতাল। হৃদরোগে আক্রান্তদের ৮০ ভাগ রোগীর চাপই এই হাসপাতালে। এই চাপ সামলাতে গিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে হিমশিম খেতে হয়। হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক ডা. ওয়াদুদ চৌধুরী জানান, গত চার বছরে এই হাসপাতালে ভর্তি রোগী বেড়েছে ৮২ শতাংশ। সেই সঙ্গে বেড়েছে মৃত্যুও। ১ হাজার ২৫০ বেডের এ হাসপাতালে গড়ে রোগী ভর্তি থাকছেন ১৬শ জন। এতে প্রতিনিয়ত বাড়তি রোগীর জরুরি চিকিৎসা পেতে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।
সারাদেশের ক্যানসার রোগীর ভরসা জাতীয় ক্যানসার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল। এর অবস্থাও করুণ। ক্যানসার ইনস্টিটিউটে ১২ হাজার থেকে ১৫ হাজার টাকায় রেডিওথেরাপির কোর্স সম্পূর্ণ করা হয়- যা প্রাইভেট হাসপাতালে শেষ করতে প্রায় ১ থেকে দেড় লাখ টাকা লাগে। তাই রোগীর চাপ এখানে বেশি। কিন্তু প্রায়ই হাসপাতালের রেডিওথেরাপির মেশিন নষ্ট থাকে। দূরদূরান্ত থেকে আসা রোগীরা থেরাপির জন্য সিরিয়াল পান না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ঘুরতে হয় সিরিয়াল পাবার জন্য। ফলে হাজারো রোগী চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হন। হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক ডা. জাহাঙ্গীর কবির বলেন, ৫শ বেডের এই হাসপাতালে সারাদেশ থেকে প্রতিদিন এক হাজার রোগী চিকিৎসা নিতে আসেন। হাসপাতালে আসা রোগীদের ভর্তির জন্য ১০ থেকে ১৫ দিন অপেক্ষা করতে হয়।
জাতীয় কিডনি হাসপাতালেও প্রায় সময় বন্ধ থাকে ডায়ালাইসিস সেবা। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন দূরদূরান্ত থেকে আসা কিডনি ডায়ালাইসিসের রোগীরা।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাসপাতালও ক্লিনিক শাখা পরিচালক ডা. আবু হোসেন মো. মঈনুল আহসান জানান, একজন চিকিৎসককে তার সক্ষমতার চেয়ে তিন-চারগুণ কাজ করতে হচ্ছে এতে চাপ বেড়ে যাচ্ছে। এর ফলে রোগীদের যে সেবা দেয়ার কথা তা দিতে পারছে না।
জনস্বাস্থ্যবিদরা বলছেন, রোগীদের ভোগান্তির অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে প্রাথমিক পরামর্শের জন্য রোগী কোথায় যাবেন, কোন চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে সেবা নেবেন, কতটুকু অসুস্থ হলে কোন পর্যায়ের হাসপাতাল কিংবা বিশেষজ্ঞের কাছে যাবেন- নেই এ সংক্রান্ত কোনো গাইডলাইন। এতে বেশির ভাগ সময়ই রোগী ভুল করে অন্য রোগের বিশেষজ্ঞের কাছে চলে যান। এ অবস্থা নিরসনে চিকিৎসাক্ষেত্রে স্ট্রাকচারাল রেফারেল পদ্ধতি চালুর ওপর গুরুত্ব দেয়ার কথা বলছেন চিকিৎসকরা।
মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের হৃদরোগ বিভাগের আবাসিক চিকিৎসক ডা. দেবাশীষ সাহা বলেন, কোনো জরুরি বিভাগের রোগী যদি বহির্বিভাগে চলে যায় স্বাভাবিকভাবেই তার চিকিৎসা পেতে দেরি হবে। এখানে যদি এরিয়া ভাগ করে রেফারেল পদ্ধতি চালু করা যায় তাহলে এই সমস্যা দূর হবে।
জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ মুহাম্মদ আব্দুস সবুর বলেন, ডাক্তাররা বলছেন- আমরা অতিরিক্ত প্রেশারে আছি, রোগীদের সময় দিতে পারছি না। তার কারণ সকাল ৮টা থেকে আড়াইটার সময় চলে এসেছে ১১টা থেকে দেড়টা এতে রোগীর সমস্যা ঠিক মতো শুনেন না। ডাক্তারদের কাজ শুধু প্রেসক্রিপশন লেখা না। দিনে দিনে রোগীর সংখ্যা বাড়লেও পর্যাপ্ত জনবল কখনোই পায়নি সরকারি হাসপাতালের বহির্বিভাগ। এতে কাঙ্ক্ষিত সেবা থেকে বঞ্চিত হন দূরদূরান্ত থেকে আসা রোগীরা।
সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব মো. সাইদুর রহমান বলেছেন, সরকারি হাসপাতালে চাকরি যাওয়ার ভয় না থাকায় সেবাগ্রহীতারা কাক্সিক্ষত সেবা পান না। এজন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিতের তাগিদ দেন তিনি।