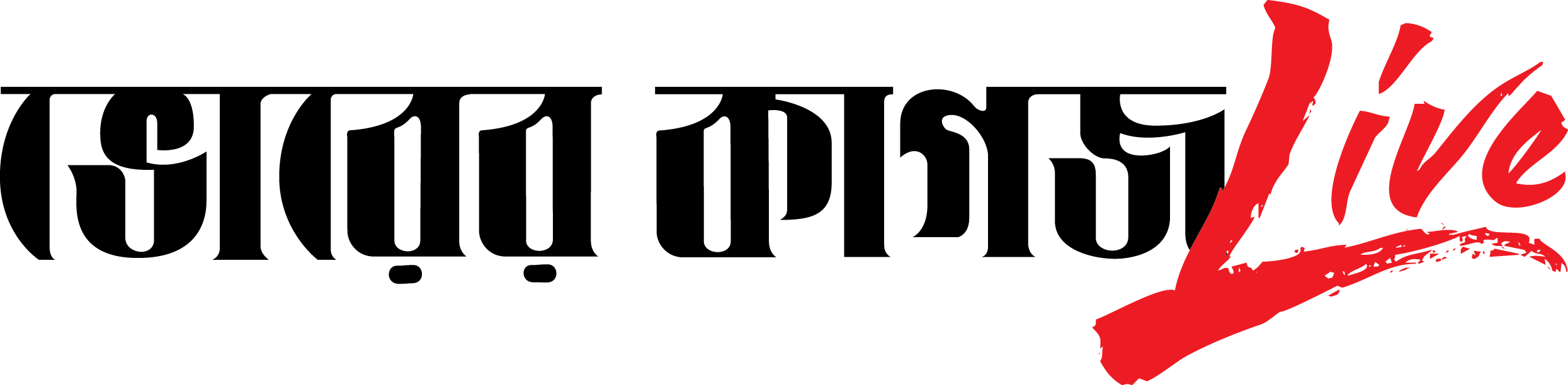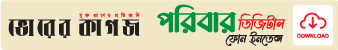যেসব উপায়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মিথ্যা সংবাদ চিহ্নিত করবেন
স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশ: ৩১ জুলাই ২০২৪, ০৪:২২ পিএম

যেকোনো মিথ্যা সংবাদ সোশ্যাল মিডিয়ায় আসা মানেই ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে যাওয়া । । ছবি: সংগৃহীত
বর্তমান সময়ে ইন্টারনেটভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একটি অপরিহার্য বিষয় হয়ে উঠেছে। এমন অনেকেই আছেন যে প্রয়োজনীয় নানা তথ্য ও সংবাদের জন্য মূলধারার সংবাদমাধ্যেমের চেয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ওপর বেশি আস্থা রাখেন। ইদানিং বিষয়টি সব শ্রেণী পেশার মানুষের মধ্যে রীতিমত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে ।
কারণ কিছু হলে বা ঘটলেই সে বিষয়টি জানতে ও যাচাই বাছাই করতে বেশি ভাগই আগে ঢুঁ মারেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। কিন্তু সেটি অনেক ক্ষেত্র ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য নেতিবাচক পরিণতি ডেকে আনতে পারে। কারণ, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যে কেউ তার ইচ্ছেমতো তথ্য শেয়ার করতে পারেন। আর এই সুযোগটি নিয়েই অনেকেই ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর নির্দিষ্ট এজেন্ডা বাস্তবায়নে মিথ্যা কিংবা বিকৃত তথ্য ছড়িয়ে দেন। তাই, সত্য সংবাদের উৎস হিসেবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ওপর নির্ভর না করেতই পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের।
সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের লাফবরাহ ইউনিভার্সিটির দুই গবেষক অ্যান্ড্রু চ্যাডউইক এবং ক্রিস্টিয়ান স্টেট এ বিষয়ক একটি গবেষণা চালিয়েছেন। গবেষণা প্রতিবেদনে তারা উল্লেখ করেন, বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যবহারকারীরা প্রতিনিয়ত ভুল ও অসত্য তথ্যের শিকার হন।
তাই ‘অসত্য খবর’ চিহ্নিত করার পন্থাগুলো জানা থাকা প্রয়োজন। সাধারণত দুই ধরনের অসত্য খবর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এই দুই গবেষক ব্যাখ্যা করেন, একটা হল ‘মিসইনফরমেইশন’ বা ভুল তথ্য অন্যটি হল ‘ডিসইনফরমেইশন’ বা রটনা বা গুজব।
‘মিসইনফরমেইশন’ বা ভুল তথ্য
কোনো ব্যক্তি বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নির্দিষ্ট কোনো পেইজ থেকে ‘মিসইনফরমেইশন’ বা ভুল তথ্য প্রকাশ করার পেছনে কোনো উদ্দেশ্য থাকে। সাধারণত প্রতারণা ষড়যন্ত্র মূলক তথ্য, বানোয়াট প্রতিবেদন বা ব্যাঙ্গাত্মত তথ্য দিয়ে এটা করা হয়। সাধারণত কোনো জনমত গড়ার উদ্দেশ্যে এই ধরনের ভুল তথ্য প্রকাশ করা হয়।
‘ডিসইনফরমেইশন’ বা গুজব
অন্যদিকে ‘ডিসইনফরমেইশন’ বা গুজব ছড়ানোর প্রধান উদ্দেশ্যই থাকে ঠকানো। আর সাধারণত ভুল তথ্য ছড়ানোর কৌশলগুলোই এই ক্ষেত্রে ফলানো হয়। যে কোনো ধরনের অসত্য খবর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আসা মানে ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে যাওয়া। কারণ অনেক মানুষই তথ্য যাচাই বাছাই না করে ‘শেয়ার’ করা শুরু করেন। তাই এই গবেষকরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভুল তথ্য যাচাই করার ক্ষেত্রে কয়েকটি নজর দেয়ার প্রয়োজন মনে করেন।
ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট
যদি ফলো করা কোনো ব্যক্তির দেয়া তথ্য নিয়ে সন্দেহ জাগে তবে তাকে প্রশ্ন করা এবং সেই হিসেবে যাচাই করা যেতেই পারে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সাধারণত মানুষের ব্যবহারের পরিধির ওপর নির্ভর করে চলে, এখানে ভুল তথ্য বা গুজব গণনা করা সম্ভব নয়। তাই অসত্য খবর চিহ্নিত করতে কিছু প্রশ্ন সাহায্য করতে পারে।
১. যিনি তথ্যটি ‘শেয়ার’ করছেন সেটা কি ব্যক্তিগত আবেগ নাকি পেশাদার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে করছেন?
২. কনটেন্টটি কোনো বিষয়ের দিকে নজর দিচ্ছে।
৩. তথ্যগুলো কি যুক্তিসঙ্গত?
৪. খবরে বিশ্বাসযোগ্য কোনো উৎসের কথা বলা আছে কি-না?
৫. যে অ্যাকাউন্ট থেকে শেয়ার করা হচ্ছে, তার জন্য সেটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ?
ব্যবসায়িক বা পেশাদার অ্যাকাউন্টস
বর্তমানে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য সফল করতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করা নতুন কিছু নয়। আর এটা প্রচারণার একটা কৌশল হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে অনেকে সময় সর্বসাধারণকে অনেক সময় নির্দিষ্ট ক্রেতা শ্রেণিকে চিহ্নিত করে তথ্য প্রচার করা হয়।
তাই কোনো বিষয়ে প্রচারণামূলক তথ্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঘোরাঘুরি করলে জানার চেষ্টা করতে হবে, সেটা আপনার প্রয়োজন? বাজারে কি এরকম পণ্য আরও আছে? সেগুলোর সাথে এগুলোর কার্যকারিতায় পার্থক্য কোথায়? সেবা বা পণ্য প্রদান করতে গিয়ে, ক্রেতার ব্যক্তিগত তথ্য নেয়া হচ্ছে কি-না?
এক্ষেত্রে জনস হপকিন্স ইনফরমেশন সোসাইটি ইন্সটিটিউট’য়ের নিরাপত্তা বিষয়ক জ্যেষ্ঠ প্রকৌশলী জোয়ি ক্যারিগান বলেন, বিশ্বস্ত ও আস্থাযোগ্য মিডিয়ার উৎসের তালিকা করে রাখা উচিত।
আরো যেসব বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে
যুক্তরাজ্যের জনস হপকিন্স ইনফরমেশন সোসাইটি ইন্সটিটিউটের নিরাপত্তা বিষয়ক জ্যেষ্ঠ প্রকৌশলী জোয়ি ক্যারিগান বলেন, বিশ্বস্ত ও আস্থাযোগ্য মিডিয়ার উৎসের তালিকা করে রাখা উচিত।
বিশ্ববিদ্যালয়টির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে তিনি আরো বলেন, খবর-প্রতিবেদন এবং ব্যক্তিগত অভিমতের পার্থক্য করতে হবে। অনেক সময় সংবাদপত্রগুলো নানান মানুষের মতামত প্রকাশ করে। যেকোনো পেশাদার উন্নতমানের সংবাদ সংস্থা তাদের প্রতিবেদন ও অন্যদের মতামত আলাদাভাবে প্রকাশ করে। এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।
এছাড়া বিভিন্ন “ফ্যাক্ট চেকিং টুলস” ব্যবহার করেও তথ্য যাচাই করা সম্ভব উল্লেখ করে ক্যারগান বলেন, এই ধরনের টুলসগুলো মিথ্যা খবর চিহ্নিত করতে সহায়তা করে। তবে মনে রাখতে হবে-এই সময়ে চোখের দেখা মানেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।
এদিকে “এআই” নির্ভর ছবি, “ডিপ ফেইক” করা ভিডিও ব্যবহার করে ভুল তথ্য প্রচার করাও এখন অনেক বেড়ে গেছে।
বিষয়টি নিয়ে ক্যারিগান বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যাই আসুক সবই তীক্ষ্ণ নজরে সন্দেহ নিয়েই দেখতে হবে। যেকোনো খবর দেখেই ঝাঁপিয়ে পড়ে বিশ্বাস করা যাবে না।