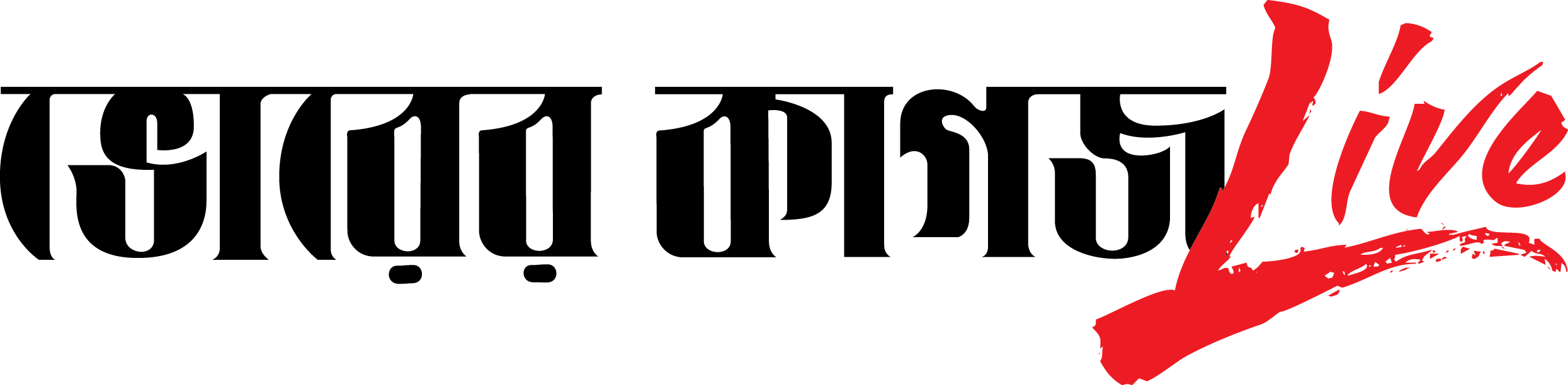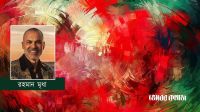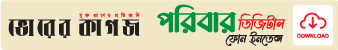খেলাপি ঋণের বেড়াজালে দেশের আর্থিক খাত, সমাধানের পথ কী?
সাইফুল ইসলাম শান্ত
প্রকাশ: ১৩ আগস্ট ২০২৫, ০৪:২৪ পিএম

খেলাপি ঋণের বেড়াজালে দেশের আর্থিক খাত নিয়ে লিখেছেন সাইফুল ইসলাম শান্ত
বাংলাদেশের আর্থিক খাত বর্তমানে এক গভীর সংকটের মুখোমুখি—এ সংকটের নাম খেলাপি ঋণ। বছরের পর বছর অব্যবস্থাপনা, রাজনৈতিক প্রভাব, দুর্বল তদারকি এবং ঋণ আদায়ে শিথিলতার ফলে খেলাপি ঋণ এখন এমন এক ভয়ঙ্কর মাত্রায় পৌঁছেছে, যা দেশের অর্থনীতির জন্য এক ধরনের “বিষফোঁড়া” হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যাংক খাতের এই অচলাবস্থা শুধু বিনিয়োগকারীদের আস্থা নষ্ট করছে না, বরং সাধারণ মানুষের সঞ্চয় ও ভবিষ্যৎ নিরাপত্তাকেও হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। প্রশ্ন হলো—এই বেড়াজাল থেকে বাংলাদেশ কতটা বের হতে পারবে?
ব্যাংক খাতের সাম্প্রতিক হিসাব বলছে, দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো খেলাপি ঋণ ৫ লাখ কোটি টাকার সীমা অতিক্রম করেছে। দুই বছর আগেও এই ঋণের পরিমাণ ছিল অনেক কম। খেলাপি ঋণ দ্রুত বৃদ্ধির পেছনে কয়েকটি বড় কারণ আছে—যেমন, ঋণ বিতরণে অনিয়ম, দুর্নীতি, ঋণগ্রহীতার ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তদারকির ঘাটতি।
বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ তথ্যমতে, ২০২৫ সালের জুন শেষে খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫ লাখ ৩০ হাজার ৪২৮ কোটি টাকা—যা ব্যাংক খাতের মোট ঋণের প্রায় ৩০ শতাংশ। মাত্র তিন মাসে এ খেলাপি ঋণ বেড়েছে ১ লাখ ১০ হাজার কোটি টাকা। আর গত এক বছরে ঋণ বেড়েছে ৩ লাখ ১৯ হাজার কোটি টাকা, প্রবৃদ্ধির হার ১৫১ শতাংশ। ২০২৪ সালের জুনে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ২ লাখ ১১ হাজার ৩৯২ কোটি টাকা। এমনকি চলতি বছরের জানুয়ারি–জুন সময়েও ঋণ বেড়েছে ১ লাখ ৮৪ হাজার ৬৬৩ কোটি টাকা বা ৫৩ শতাংশ।
অর্থনীতিবিদদের মতে, ব্যবসা-বাণিজ্যে স্থবিরতা, শিল্পখাতের দুরবস্থা, উদ্যোক্তাদের কারাবরণ বা বিদেশে পলায়ন, আর ব্যাংকের কাঙ্ক্ষিত আদায় না হওয়াই এই ঋণ বৃদ্ধি ঠেকাতে ব্যর্থ হচ্ছে।
খেলাপি ঋণের এই বিস্তার শুধু ব্যাংকগুলোর সুনাম নষ্ট করছে না বরং পুরো অর্থনীতির সঞ্চালন ব্যবস্থাকেই দুর্বল করে দিচ্ছে। ব্যাংকের মূলধন কমে যাওয়ায় নতুন বিনিয়োগের সুযোগ সংকুচিত হচ্ছে, কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বাধা তৈরি হচ্ছে, এমনকি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আস্থাও কমে যাচ্ছে।
এই সঙ্কট কেন তৈরি হলো
খেলাপি ঋণ বৃদ্ধির পেছনে কোনো একক কারণ নেই বরং নীতিগত পরিবর্তন, অর্থনৈতিক ধাক্কা এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থার অন্তর্গত দুর্বলতার সমন্বয়ে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। প্রথমত, ঋণ খেলাপি হিসেবে শ্রেণীকরণ করার সময়সীমা ও রেকগনিশনে নতুন কাঠামো হয়েছে — আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর চাপে নীতিনির্ধারণীরা দ্রুত স্বচ্ছতা আনার চেষ্টা করেছেন, ফলে আগে গোপনে রাখা অনেক ‘স্টেসড’ অ্যাসেট এখন আনুষ্ঠানিকভাবে খেলাপি হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। এই পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবেই খেলাপি ঋণের পরিসংখ্যানকে ঊর্ধ্বমুখী করেছে।
গত বছরের আগস্টে সরকার পরিবর্তনের পর আওয়ামী লীগ–সমর্থিত ব্যবসায়ীদের অনেকের ব্যবসা স্তিমিত হয়ে পড়েছে—এসব প্রতিষ্ঠানের ঋণ খেলাপি হয়ে পড়েছে। আগে যেসব ঋণ বিশেষ ব্যবস্থায় নিয়মিত করা হয়েছিল, তা শোধ না হয়ে আবার খেলাপি হয়ে পড়ছে। ব্যাংকগুলো এখন সব ঋণের প্রকৃত চিত্র দেখানো শুরু করছে। এতেই বাড়ছে খেলাপি ঋণ।
দ্বিতীয়ত, অর্থনীতির নির্দিষ্ট সেক্টরে মন্দা— নির্মাণ, শিল্প এবং কয়েকটি বড় কর্পোরেট গ্রুপের কস্ট-ডিফল্ট— ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তৃতীয়ত, কিছু ব্যাংকের কর্পোরেট গভার্ন্যান্স দুর্বল; নজরদারি, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় ফাঁক রয়েছে। চতুর্থত, প্রভিডেন্ট প্রভিশনিং-এ ঘাটতি ও ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদ দ্রুত মিটিগেট না করার কারণে ব্যাংকগুলোর ক্যাপিটাল কভারেজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
এসব সমস্যার অর্থনৈতিক পরিণতি স্পষ্ট — ব্যাংকগুলো নতুন কিস্তি দিতে আগ্রহী না, বিনিয়োগে ধীরগতি, আর বাস্তব অর্থনীতির ছোট-মধ্যম যেমন উদ্যোগগুলো ঋণ পাওয়ায় বাধার সম্মুখীন। এতে কর্মসংস্থান, রপ্তানি সক্ষমতা এবং সার্বিক প্রবৃদ্ধি ঝুঁকির মুখে পড়ে।
সমাধানের পথ কী?
১) স্বচ্ছতা ও দ্রুত নীতিগত ব্যবস্থা গ্রহণ: প্রথম শর্ত হলো ঘটনার স্বচ্ছতা চিহ্নিতকরণ। ব্যাংকগুলোকে সময়মতো ও পুরোপুরি খেলাপি ঋণ রিপোর্ট করতে হবে; কেন্দ্রীয় ব্যাংককে নিয়মিত ও প্রকাশ্য পরিসংখ্যান দিতে হবে যাতে নৈতিক সাবধানতা ফেরাতে পারে। পাশাপাশি খেলাপি শ্রেণী নির্ধারণ ও প্রভিডেনশিয়াল রিকোয়ারমেন্টের নিয়মগুলোকে বাস্তবধর্মী ও কার্যকরী করে তুলতে হবে।
২) অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি গঠন: অনেকে সুপারিশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্তরে বা পাবলিক-প্রাইভেট অংশীদারিত্বে একটি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি গঠন করতে — যেখানে দোষী ঋণগুলো সংগৃহীত করে শ্রেণীবদ্ধভাবে পুনর্গঠন, বিক্রি বা পুনরায় রিকভারি করা হবে। অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি ব্যাংকগুলোর ব্যালান্সশিটে ক্লিয়ারিং এনে ব্যাংকগুলোর ক্রেডিট প্রদানের ক্ষমতা দ্রুত বাড়াতে সাহায্য করবে।
৩) শক্তিশালী গভার্ন্যান্স ও ফরেনসিক অডিট: বড়-বড় কেসে কর্পোরেট অথবা ব্যাংক-অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি আছে কিনা তা তদন্ত করতে স্বাধীন ফরেনসিক অডিট অবিলম্বে চালু করা দরকার। ব্যাংক পরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বোর্ড-লেভেলে প্রকৃত পেশাদার নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা উচিত। সরকারি প্রভাব বা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ সীমিত করতে সুনির্দিষ্ট আইনগত ও প্রশাসনিক বাধ্যবাধকতা প্রণয়ন প্রয়োজন।
৪) ঋণ পুনর্গঠনে উদার কিন্তু শর্তসাপেক্ষ নীতি: দুর্বল কিন্তু পুনরুজ্জীবনযোগ্য ব্যবসার ক্ষেত্রে রিস্ট্রাকচারিং ও পুনর্গঠন প্রদানের জন্য স্পষ্ট নিয়মানুবর্তিতা তৈরি করা দরকার—কিন্তু এটি লঘু-দণ্ড নয়; কড়া শর্তে কাজ করতে হবে যাতে জবাবদিহিতা বজায় থাকে। একই সঙ্গে রিস্ক-অ্যাসেসমেন্ট ও কাস্টমার-ব্যবহার-মনিটরিং বাড়াতে ব্যাংকগুলোকে প্রযুক্তি ও দক্ষতা ক্রয় করতে উৎসাহিত করতে হবে।
৫) ব্যাংকিং সেক্টরে কনসোলিডেশন ও রিক্যাপিটালাইজেশন: দুর্বল রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর জন্য সমন্বয় ও সম্ভাব্য মার্জারের পথে এগোনো যেতে পারে; সেখানে সরকারের কড়া শর্তে রিক্যাপিটালাইজ করে পরিচালনায় পেশাদারিত্ব আনা যেতে পারে। একই সঙ্গে বেসরকারি ব্যাংকগুলোতেও ক্যাপিটাল-অফারিং ও স্ট্রেস-টেস্ট একাধিকবার করা উচিত।
৬) ক্ষুদ্র ও মধ্যম উদ্যোক্তা (SME) সুরক্ষা: দেশের জাতীয় অর্থনীতির মেরুদণ্ড SME সেগমেন্ট; তাদের জন্য সহজ শর্তে গ্যারান্টি ও টেকসই ঋণ নিশ্চিত করা গেলে অর্থনীতি দ্রুত চাঙ্গা হবে এবং বাকিদের উপর চাপও কমবে।
খেলাপি ঋণ শুধু একটি আর্থিক সমস্যা নয়, এটি দেশের অর্থনৈতিক স্বপ্নকে থামিয়ে দেওয়ার মতো বড় হুমকি। এখনই যদি কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া যায়, তবে এই ফাঁদ থেকে বের হয়ে ব্যাংক খাতকে আবারও গতিশীল করা সম্ভব। না হলে, এই ঋণের বেড়াজাল দেশের অর্থনীতিকে দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির মুখে ঠেলে দিতে পারে। এখনই সময় স্বচ্ছতা, সুশাসন ও কঠোর তদারকি নিশ্চিত করার। তাহলেই খেলাপি ঋণের বেড়াজাল থেকে বের হয়ে বাংলাদেশ আবারও অর্থনৈতিক গতিশীলতা ফিরে পাবে।